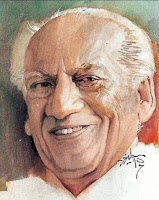বিংশ শতাব্দির কবিরা অভাবিত কিছু জায়গা থেকে
উঠে এসেছেন। ‘ফয়েজ’এর পূর্বপুরুষেরা পাঞ্জাবের চাষী ছিলেন। সেই পাঞ্জাব – মধ্য এশিয়া
ও ভারত মহাসাগরের মাঝে, পর্বতমালা ও মরুভূমির মাঝে মহামরুদ্যান! তাঁর বাবা যাযাবর ছিলেন
– কিছু পয়সা রোজগারের মুখ দেখেছিলেন এবং আফগানিস্তানে গিয়ে সামন্ত যুবদের কিছু কিছু
অভ্যাস রপ্ত করেন। তারপর রাজার সাথে তাঁর ঝগড়া হয় – ছদ্মবেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন
আফগানিস্তান ছেড়ে। চলে যান ইংল্যান্ডে। কেম্ব্রিজে, ‘লিঙ্কন্স ইন’এ পড়াশুনো করেন। শেষে
একজন আইনজীবী হয়ে ফিরে আসেন নিজের জন্মস্থানে। ফয়েজ যদি বংশানুক্রমে এই যাযাবর প্রবৃত্তি
পেয়েও থাকেন তবে সেটা চিত্তের অভিসারে; বড় হওয়ার অনেক পর অব্দি তাঁর নিজের প্রদেশ ছেড়ে
দূরে কোথাও যাওয়ার সুযোগ হয় নি। বোধহয় তাঁর পক্ষে ভালোই হয়েছিল যে তিনি ইয়োরোপে পড়তে
যান নি। উনিশশো তিরিশের দশকের ভাবনাচিন্তাগুলো কোনো না কোনো ভাবে তিনি ঘরে বসেই আয়ত্ত
করতে থাকেন – বইয়ের মাধ্যমে, গোপনে হাতে আসা প্যাম্ফলেটের মাধ্যমে, যাত্রীদের কাছে
শোনা কাহিনীর মাধ্যমে আর সেই অস্পর্শনীয় কিন্তু সমৃদ্ধ দৈত্যটির মাধ্যমে যাকে যুগসত্ত্বা
বলা হয়ে থাকে। তাঁর নিজের মাটিতে এসব ভাবনাচিন্তাগুলো তাঁর মধ্যে শিকড় গাড়ে আর পরিচিত
সূর্যালোকে এসবের শরীর ও ছায়া তিনি দেখতে পান।
ফয়েজ লাহোরে পড়াশোনা করলেন এবং সময়কালে অমৃতসরে
কোনো বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করলেন। এই দুটো শহরের মাঝে তখন কোনো বিভাজক সীমারেখা ছিল
না। ফয়েজের দিন কাটতে লাগল কফিহাউজে, ব্রডকাস্টিং স্টুডিওতে এবং চন্দ্রালোকিত বনভোজনে।
আপাতদৃষ্টিতে সবই খুব অগভীর। পদ্যকার হিসেবে খুব তাড়াতাড়ি তিনি সেই সব অসংখ্য উঠতি
কবিদের থেকে আলাদা হয়ে যেতে পেরেছিলেন, প্রতিটি বছর যাদের একরাশ নতুন প্রজন্ম উঠে আসে।
আবার কিছু কবিদের চেহারায়, পোষাকে যেমন একটা কবি-ছাপ থাকে, ফয়েজ তাদের থেকেও আলাদা
ছিলেন। ভদ্র, সহজ মানুষ, ক্রিকেট-প্রেমিক এবং সবসময়, নিজে কথা বলার চেয়ে অন্যকে কথা
বলতে দিতে বেশি তৈরি। এটা তাঁর বিশেষত্ব ছিল যে কয়েকজন বন্ধুদের মাঝে হোক বা কলেজের
বড় শ্রোতৃসমাবেশে হোক, কবিতা আবৃত্তি করতে হলে শান্ত, আবেগশূন্য কন্ঠে পড়ে যেতেন। কক্ষনো
ওই ধরণের আবেগদৃপ্ত মন্ত্রোচ্চারের ভঙ্গী ব্যবহার করতেন না, যা ব্যবহার করে বস্তাপচা
ছড়া অথবা অন্তঃসারশূন্য আবেগকেও ভাবগম্ভীর দেখানো যায়।
ফয়েজের প্রথম কবিতার বইয়ের সুন্দর প্রথম চতুস্পদীটি
প্রথম লিখিত নয়। শুরু করেছিলেন চিরাচরিত ধরণে; কাল্পনিক এক প্রেয়সীর নিষ্ঠুরতায় দীর্ঘশ্বাস
তুলে – সে নারী আবার জোসেফ কনরাডের নায়িকার মত প্রায়-অশরীরী – অথবা মদের বোতলটির মোহিনী
রূপের প্রশস্তি গেয়ে। তাঁর ক্ষেত্রে এসব বরং কম কাল্পনিক ছিল। বন্ধুদের বকবকানির চোটে
বা কুঁড়েমির জন্য যখন একটা অসমাপ্ত পদের সুর হারিয়ে যেত অথবা এক ঘন্টা বাদে পড়বার জন্য
কিছু পংক্তি খসড়া করতে হত এক কোনে বসে, তখন সত্যিই হয়ত এসবের প্রয়োজন হত। যদিও পাঞ্জাব
তখন ঘটনাবিহীন, ভূমিবেষ্টিত পোতাশ্রয়, ইতিহাসের জোয়ার এসে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছিল বাইরের
জগৎ আর সেই জোয়ারের প্রান্তিক ঢেউগুলো মাল রোডে, কাশ্মিরি গেটে, লরেন্স গার্ডেনে পৌঁছে
যাচ্ছিল। ফয়েজের কাব্যের অন্তর্বস্তু সত্বর রাঙিয়ে উঠছিল দেশাত্মবোধে, তারপর আরো সত্বর
সমাজবাদী অনুভবে। কল্পনাশক্তির সাথে সাথে তাঁর মধ্যে সহজাত ছিল বাস্তবকে চেনার শক্তি।
তিনি বুঝতেন যে কবি সে নাগরিকও বটে। প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘে অংশগ্রহণ করতেন, স্থানীয়
শ্রমিকদের সাথে পরিচয় ঘটল তাঁর; সন্ধ্যেগুলো কাটতে লাগল তাদের দলগুলোকে পড়া, লেখা ও
সমাজবাদের সুত্রগুলো শিখিয়ে।
যুদ্ধ আসার আগে ফয়েজ সাহিত্যে নিজের জায়গা
করে নিয়েছিলেন; যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলি রাজনৈতিক ইতিহাসেও তাঁর জায়গা করে দিল।
জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের পর যখন দুনিয়ার ভারসাম্য পাল্টে গেল, ফয়েজ যুদ্ধটিকে
মানবমুক্তির যুদ্ধ হিসেবে দেখলেন এবং সরকারি চাকরিতে ঢুকলেন। যুদ্ধপরবর্তী দিনে তিনি
নিজের এই খোলস থেকে বেরিয়ে খোলাখুলিভাবে রাজনীতিতে এলেন। মুসলিম লীগের কট্টর সমর্থক
তিনি কখনোই ছিলেন না। তাঁর অভিমত ছিল যে দেশভাগের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে স্মৃতি থেকে মুছবার
একমাত্র রাস্তা হল সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামে নতুন রাষ্ট্রটিকে গড়ে তোলা।
কিছুদিনের মধ্যেই স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। মুসলিম লীগ ধুয়ে মুছে যায়। প্রতিশ্রুত স্বর্গ, জমিদার
আর উচ্চাভিলাষীদের জন্য বইতে থাকা দুধ আর মধুর বন্যার একটি নরকে পরিণত হয়। এই
স্বপ্নভঙ্গ ফয়েজের সুন্দরতম কবিতাগুলির একটিতে পঁচিশটি নিখুঁত পংক্তিতে বিধৃত রয়েছে।
ইতিমধ্যে ফয়েজ লাহোর থেকে প্রকাশিত ‘পাকিস্তান
টাইমস’এর সম্পাদক হয়েছেন। গদ্য এবং পদ্য, দুয়েতেই দেশের প্রতিক্রিয়াশীল প্রবৃত্তিগুলির
ওপর হামলা চালাচ্ছেন। দেশের বাইরের প্রগতিশীল চিন্তাগুলির প্রতি তাঁর সমর্থনও পুরোদমে
চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজের হাতে খবরের কাগজটাকে এমন করে গড়ে তুললেন যে কাগজে মুদ্রিত মতামতগুলো
সারা দুনিয়ায় সবাই জানতে শুরু করল এবং উদ্ধৃত করতে লাগল। বৃটিশ প্রেস মাঝে মধ্যেই ব্যাজার
মুখে পাকিস্তান টাইমসএর মতামত উদ্ধৃত করত। তা সত্ত্বেও যখন ভোটের ঠিক আগে ৯ই মার্চ
১৯৫১ তারিখে ফয়েজকে আরো বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তির সাথে হঠাৎ
গ্রেপ্তার করা হল, ‘লন্ডন অবজার্ভার’ একটি ‘চমৎকার’ খবরের কাগজ হিসেবে ‘পাকিস্তান টাইমস’এর
নাম নিল। সম্পাদকের প্রশংসা করল “ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে তীব্রতম ঘৃণার বাতাবরণকে
উপেক্ষা করে মহাত্মা গান্ধীর শেষকৃত্যে লাহোর থেকে বিমানে উড়ে যাওয়ার মত বুকের পাটা
রাখা সাহসী ব্যক্তি” হিসেবে। ‘লন্ডন অবজার্ভার’এর সাংবাদিক এটুকুতেই থেমে থাকলেন না।
বললেন, “মুসলিম লীগের সদস্যেরা ফয়েজকে যে ঘৃণা করে, তা ওদের দুর্বলতাগুলো এত তিক্ত,
স্পষ্ট ভাবে তিনি দেখিয়ে দেন বলে, কম্যুনিস্টদের প্রতি তাঁর দরদের জন্য নয়”।
১৯৫৫ সাল অব্দি ফয়েজ জেলে ছিলেন। দীর্ঘকাল
মৃত্যুদন্ডের খাঁড়া তাঁর ওপর ঝুলেছিল। তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর এসবের প্রভাব পড়ল। পড়ার
জন্য চশমা পরতে হল। তা সত্ত্বেও পড়া তিনি চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন এবং বহুদিন যাবৎ প্রতিশ্রুত
উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসের জন্য সামগ্রী জোটাতে পেরেছিলেন। এমনকি সুদূর স্কটল্যান্ড
থেকে বীজ আনিয়ে ফুল চাষ করার চেষ্টাও তিনি করলেন। উর্দু কবিরা, যাঁরা লাগাতার ফুলের
কথা লিখতে কখনো হাঁপান না, প্রায়শ কিছুই জানেন না ফুলের বিষয়ে। এখানেও বোধহয় ফয়েজের
বাস্তবতাবাদের বোধ নিজেকে জাহির করছিল, যদিও ফয়েজের সঙ্গী কয়েদীটি নিজের বাগানের জমিতে
মুর্গীপালন করে নিঃসন্দেহে বাস্তববাদকে আরো বেশি ব্যবহারিক রূপ দিচ্ছিল।
সবচেয়ে বড় কথা যে ফয়েজ, জেলে থাকাকালীন যথেষ্ট
পরিমাণে – তাঁর নিজের মাপে – কবিতা লিখতে এবং প্রকাশিত করাতে পারছিলেন। লেখার মধ্যে
দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শগুলি কঠোর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মিশেল পেয়ে নতুন শক্তিতে
বলীয়ান হয়ে উঠছিল। সরকার তাঁকে অস্পষ্ট কিন্তু অতিনাটকীয় কিছু অভিযোগে অভিযুক্ত করা
সত্ত্বেও নতুন কবিতাগুলি প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে গিলে খাচ্ছিল লোকে। সব মিলিয়ে খুব
কমই লিখেছেন কবি। হিমালয়ের দক্ষিণে সামাজিক অস্তিত্ব, সেই সব মানুষের সময় নষ্ট করার
অদ্ভুত প্রতিভা রাখে যাদের নিজের জীবনের সময়টা নিয়ে কিছু করার থাকে। ‘ফলস্টাফ’১এর
‘ট্যাডার্ন বিল’এ রুটির সাথে বস্তার অনুপাতের মত, সামাজিক জীবন এখানে সবার ওপর সমানভাবে
কথা বলার সাথে ভাবনাচিন্তার একটা বিদঘুটে অনুপাত চাপিয়ে দেয়। সৈন্য প্রশাসনে, ফয়েজের
ওপর যুদ্ধকালীন কাজের বিরাট চাপ ছিল; ফয়েজ নালিশের সুরে বলতেন যে যখনই একটা ভালো শে’র
তাঁর মনে নাড়া দিয়ে উঠত, তখনি তাঁকে উঠে অফিসে ফিরতে হত। যুদ্ধের পর সম্পাদকীয় কাজের
টেবিলে তাঁর দাসত্ব আরো বেড়ে গেল। সাহিত্যিক দিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায় জেলের মেয়াদ
তাঁর জন্য শাপে বর ছিল।
ফয়েজ সাহিত্যের জগতে তখন এসেছিলেন যখন আধুনিক
উর্দুর মহানতম ওস্তাদ বিদায় নিচ্ছিলেন। ইকবাল নিজের দর্শনের বা স্টাইলের কোনো উত্তরাধিকারী
রেখে যান নি। তবু যদি কাউকে উত্তরসুরি বলতে হয় তাহলে অনেক দিক থেকে ফয়েজের কথাই মাথায়
আসবে। দুটো ব্যক্তিত্বের মাঝে এর বেশি তফাৎ হতে পারে না। ইকবাল নিজের সম্ভ্রান্ত একাকীত্বে
গুটিয়ে থাকা প্রথিতযশা বৃদ্ধ, ফয়েজ, লাহোরের রাস্তায় টাঙ্গায় চেপে ঘুরে বেড়ানো এক ছোকরা
যাকে কেউ চেনে না। ইকবাল নতুন প্রভাদীপ্ত ইসলামের ধর্মগুরু, ফয়েজ আজাদ-ভাবুক, মার্ক্সবাদের
দিকে পথ খুঁজে খুঁজে এগোচ্ছেন। বৃদ্ধ মানুষটির গাম্ভীর্যের আর তরুণটির উচ্ছল আনন্দময়তার
নিচে তবু একই মনোনিবেশ রয়েছে নিজেদের দুনিয়া আর শিল্পের প্রতি। কবিতাকে অলঙ্করণ হিসেবে
বা আরামদায়ক, কাজকর্মহীন কোনো পদের দিকে এগোবার সিঁড়ির হাতল হিসেবে নেওয়ার বদলে সেই
অগ্নিস্তম্ভের মত ভাবা, যা তীর্থযাত্রীদের গভীর অরণ্যে পথ দেখায়, দুজনেরই খুব স্বাভাবিক
মনে হয়েছে।
তাছাড়া, ইকবালের ধার্মিক পুনরুত্থানবাদ বিংশ
শতাব্দীতে এশিয়ার পুনরুজ্জীবনেরই অঙ্গীভূত ছিল। চলতি ধরণের জাতীয়তাবাদের সীমার বাইরে
গিয়ে ইকবাল দলিত শ্রেণী এবং জাতিগুলির বিদ্রোহের প্রচার করেছেন। যার প্রতীক্ষায় তিনি
দীর্ঘকাল রইলেন, ইসলামের সেই দীপ্ত নতুন দিন আর এল না। অন্যদিকে একটা বড় ভুখন্ড, প্রগতির
আধুনিক ঢেউটাকে আটকাবার প্রভাবশালী বাধা হিসেবে আর নেই … যা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের পশ্চিমী
পন্ডিতরা ইদানিং দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ইকবালের বাণীর ভুষিটা খসে গেছে, দানাটা – এশিয়ার
বিদ্রোহ – রয়ে গেছে; বৈপ্লবিক সমাজবাদ তার নতুন পোষাক। এই অর্থে, ঐতিহাসিক দিক থেকে
ফয়েজই ইকবালের উত্তরসুরি, ঠিক যেমন কবি হিসেবেও ইকবালের পর আসা কবিদের মাঝে ফয়েজ বিশিষ্টতম।
স্টাইলের দিক থেকে দুজনে একই ট্র্যাডিশনের।
এটা সত্যি যে ফয়েজ শুধু উর্দুতেই লেখেন, লেখার মাধ্যম হিসেবে ধ্রুপদী ফারসীতে – যে
ভাষাটির চর্চা ইকবাল এত বেশি করলেন – তাঁর রুচি পাঞ্জাবী দেশীয় ভাষার প্রতি তাঁর রুচি
থেকে বেশি নয়। তা সত্ত্বেও, কোনো কোনো মুহুর্তে যদিও ফয়েজ প্রকাশভঙ্গীতে পরম সহজ হতে
অএরেছেন, অধিকাংশ সময়ে তাঁর কাব্যভাষা ততটাই বিলক্ষণ ফারসী কিম্বা আরবী যতটা ইকবালের।
তার ওপর, দুজনেই পরম্পরাগত রূপ ও ছন্দ এবং অধিকাংশ সময়ে চিরাচরিত অর্দ্ধ-প্রতীকী রূপকল্পের
পুরোনো নমনীয় প্রণালীটি ব্যবহার করেন। দুজনেই নিছক প্রয়োগধর্মী হওয়ার জন্য প্রয়োগ করেন
না, যেমন নাকি আমাদের যুগের কিছু উর্দু লেখক এবং অনেক বেশি সংখ্যায় পশ্চিমি লেখকেরা
করে থাকেন। দুজনের মাঝের তীব্রতম বৈপরীত্য দুজনের কবিতার রঙে। ইকবাল নিজের সবচেয়ে স্বাভাবিক
ক্ষণে ব্যগ্র, অস্থির এবং সোজাসুজি কথা বলতে ভালোবাসেন, ফয়েজ সেখানে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময়,
অনুবাদ করাও বেশি শক্ত। একজনের আঁকা ছবি মনে হয় সূর্য্যালোকে দীপ্ত, আরেকজনের চন্দ্রালোকে।
এই যে একজনের সূর্য্যালোকের প্রেরণা ছিল একটি
প্রাচীন ধর্ম আর আরেকজনের চন্দ্রালোকের প্রেরণা ছিল তাঁর যুগের সবচেয়ে বৈপ্লবিক জীবনদৃষ্টি,
প্রথম দর্শনে এতে যতটা বিরোধাভাস মনে হয়, ততটা বোধহয় ছিল না। ইকবালের ‘ইসলামবাদ’ তাঁকে
আবেগে সংপৃক্ত চিন্তাধারার একটা তৈরি কাঠামো দিয়েছে; ওই ধরণের চিন্তাধারা দিয়ে ইংরেজিতেও
যেমন একজন উটকো কবিও ‘শোলোক’ লিখতে পারে আবার মিলটনের মত কবির হাতে পড়লে একখানা ‘প্যারাডাইস
লস্ট’ বেরিয়ে আসতে পারে। এধরণের কিছু ফয়েজ সমাজবাদী চিন্তাধারা থেকে পান নি। সমাজবাদের
চিন্তাভাবনাগুলো ছিল নতুন, নগ্ন, গাম্ভীর্যপূর্ণ, ইকবালের চিন্তাভাবনা থেকে অনেক বেশি
আমরা যে দুনিয়ায় বাঁচছি তার কাছাকাছি। কিন্তু ওই একই কারণে সমাজবাদের চিন্তাভাবনাগুলো
শিল্পের মত নম্র করে নেওয়া বা শিল্পের সুরে বেঁধে নেওয়া সহজ নয়, বরং কঠিন। নিষ্পত্তি
করতে ফয়েজের মন ভেঙে যেত যে কবিতা পরগাছার চাষ, যুক্তির অসঙ্গতিতে বাড়ে ভালো। অবাস্তবের
চাইতে বাস্তবের সাথে কাজ করা কল্পনার পক্ষে বেশি লাভজনক, যদিও আকচার তা খুব স্বতঃস্ফূর্ত
ভাবে হয় না। যুগটা কাঁচে নয়, গ্রানাইট পাথরে খোদাই করা যুগ, ফয়েজ একবার বলেছিলেন। যখন
ফয়েজ নিজেকে গ্রানাইটে খোদাই করার কাজে নিয়োজিত করলেন, তিনি সহজে সহজ হতে পারার আশা
ছেড়ে দিলেন। ফলতঃ, কিছু অন্ধকারে হাতড়ানো, কিছু অসফলতা, কিন্তু বিশিষ্ট নতুন কিছু হাসিল
করার সম্ভাবনাও।
এই অভিজ্ঞতা আমাদের শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
শিল্প-সমস্যার ওপর – শিল্পী এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের মাঝে সম্পর্ক – কিছুটা আলোকপাত
করে।
ফয়েজের পাঠকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন, মাঝেমাঝেই
তাঁর কবিতায় ফয়েজ এক ধরণের দ্বৈততায় ফিরে যান – যেমন ‘দুটি কন্ঠস্বর’ কিম্বা ‘দুটো
ভালোবাসা’ – যেন দুটো বিপরীত জীবনদৃষ্টি ছিল তাঁর এবং সবসময় দুটোকে তিনি মেলাতে চাইতেন।
এটা আশ্চর্য নয় যে তিনি বিভাজিত মনের যন্ত্রণায় ভুগে থাকবেন। জাতীয়তাবাদী লেখক হওয়া
সহজ, জাতীয় লেখক হওয়া কঠিন,; এবং ফয়েজ এমন একটি জাতি, সংস্কৃতি ও আকাঙ্খার সন্তান ছিলেন
যারা তখনো তাদের আত্মার সন্ধানে মগ্ন ছিল। সত্যি বলতে, পাঞ্জাবের যে মুসলমান সম্প্রদায়ে
তিনি বড় হয়েছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে ঝিমন্ত ও গতানুগতিক জীবন কাটানো মনে হলেও অস্বাভাবিক
রকম জটিলতা ও দ্বন্দ্বে জর্জরিত ছিল ওই সম্প্রদায়। এমনও বলা যায় যে উর্দু কবিতার মুখ্য
প্রেরণা আরো দক্ষিণ থেকে এই প্রদেশে এসেছিলই আরো বেশি দ্বন্দ্ব, আরো বেশি আততিতে উদ্দীপিত
হতে। নিজেদের হিন্দু প্রতিবেশীদের থেকে আধুনিক পরিস্থিতির সাথে মিশ খাইয়ে নিতে কম অভ্যস্ত
পাঞ্জাবী মুসলমানদের ব্যবহারিক বোধ ছিল কম এবং কল্পনাশীলতা ছিল বেশি; তাদের মধ্যে সবচেয়ে
বেশি জগৎ-সচেতন যারা, সূক্ষ্ম বিষয়গুলো স্পর্শ করত তাদের।
বেশির ভাগ লেখকের মত (ইকবাল ছাড়া) ফয়েজও মুসলিম
লীগের কার্যক্রমের প্রতি সন্দেহ থেকে নিজের পথ শুরু করলেন। তাঁর মনে হল যে লীগের কার্যক্রম
আধুনিক দুনিয়া ও তার সমস্যাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে সামন্ততান্ত্রিক গ্রামের জড়তায় ফিরে
যেতে চায়। অন্য দিকে যারা অখন্ড ভারতে বিশ্বাস করত তারা উর্দুকে মেঠো করে হিন্দির মধ্যে
মিলিয়ে দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং হাটবাজারের মুখের ভাষা ‘হিন্দুস্তানি’তে পরিণত করার
চিন্তা করছিল। ফয়েজের সহজাত সাহিত্যিক বোধ এধরণের সম্ভাবনার প্রতিক্রিয়ায় গুটিয়ে গিয়ে
ফয়েজকে প্রাচীন ফারসি শব্দাবলির ঘুরপথে, মধ্য এশিয়ার হৃদয়ে অবস্থিত পানপাত্র এবং মিনার,
গোলাপ-বাগিচা আর পরীদের বিলাসিতাপূর্ণ স্বপ্নজগতে টেনে নিয়ে গেল।
সব মানুষই ক্রিয়া ও ভাবনার পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির
শিকার হয়, আর বেশির ভাগ মানুষের থেকে বেশি ভোগে শিল্পীরা। ফয়েজের পরিবেশের এইসব বিপরীতমুখী
স্রোতগুলির অভিঘাত তাঁর চেতনায় যেন কর্তব্য ও ইচ্ছার, ব্যবহারিক সক্রিয়তা ও কাব্যিক
দিবাস্বপ্নের নিরন্তর দ্বন্দ্ব তৈরি করল। সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রখর ছিল বলে নিজেরই
শিল্প সম্পর্কে বিবেকশূন্য বা বীতশ্রদ্ধ হওয়ার বিপদ ছিল ফয়েজের সামনে, যেমন বোধ করি
সব সৎ সাহিত্যিকদের সামনেই থেকে থাকে। ‘যুদ্ধের কী করা উচিৎ এই সব নাচিয়ে কবিদের সাথে?’
তাঁর মাথায় দুটো ছবি একে অন্যের সাথে ধাক্কাধাক্কি করতঃ শুকিয়ে যাওয়া, রুগ্ন, সর্বস্বান্ত
মানুষ নালায় পড়ে মরছে; পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক রোমান্টিকতার আয়নায় রঞ্জিত-কপোল, কাজলকালো
আঁখিপল্লব, ক্ষীণকায়া সুন্দরী নিজের মুখটি চেয়ে চেয়ে দেখছে। এ দুটি দৃশ্যের মাঝে তিনি
জীবনের দুটো বিপরীতমুখী চুম্বক দেখতে পেতেন, একটি তাঁর ইতিবাচক, প্রগতিশীল সত্ত্বা
ধরে, অন্যটি তাঁর পশ্চাৎপদ, পুনরুজ্জীবনহীন সত্ত্বা ধরে টানছে।
ফয়েজের সৃজনপথের এই দ্বন্দ্বগুলো সব দেশের
প্রগতিশীল আন্দোলনের সাধারণ সমস্যাগুলোরই রকমফের ছিল। পুরোনো ও নতুনের দাবির মাঝে সংঘাত
(দুদলই নিজের জায়গায় ঠিক); ক্ষুধিত বর্তমান বনাম পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনা নিয়ে ভবিষ্যৎ,
অলীক কল্পনা বনাম সম্ভাব্যতা, আবেগ বনাম যুক্তি, শ্রমিক বনাম বুদ্ধিজীবী, ব্যক্তি বনাম
সমাজ, জনতা বনাম সরকার। বিশ্ববিপ্লব, বেগবান ও অনুশাসিত ভাবে কবির জীবনযাপনে ঢুকে পড়ছিল।
সমানভাবে আত্মসচেতন এবং প্রতিরোধী এক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই বিপ্লবের চাপ, কবির মনে
জাগাচ্ছিল চেতনার ওই দ্বৈরথ।
কবি নিজে এবং অন্যরা এই দ্বৈরথকে তাঁর দুর্বলতা
মনে করতে পারেন। কিন্তু এই দ্বৈরথই সেই জেদি নান্দনিক শিকড়ের প্রমাণ যা কবিকে আন্দোলনের
শক্তিশালী জোয়ারে মুছে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। অন্য অনেকেই বাঁচতে পারেনি। সমস্ত
মহান ও বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনের মত আমাদের যুগের এই বিপ্লবেরও সহজ প্রবৃত্তি ছিল নারীপুরুষদের
নিজের সৈন্যদলের একক, নিজের হিসেবের সংখ্যা করে নেওয়ার; নিজের ও তাদের, দুতরফেরই ক্ষতি
করেও। ব্যক্তি কেউ নয়, উদ্দেশ্যই সব, ১৭৯৩ সালে জ্যাকোবিনরা বলেছিল। দুনিয়াকে পাল্টে
দেনেওয়ালা সবাই তবে থেকে ওই কথাটিরই প্রতিধ্বনি করে আসছে। যাদের সাথে ফয়েজের সম্পর্ক
হয়েছিল, তারা তখন একপাথুরে দলের, এমন একটি সংগঠনের ফর্মুলা গড়ে তুলছিল যার প্রতিটি
সদস্য পুরোপুরিভাবে ওই দলেরই পরিচয়ে পরিচিত হবে – পরবর্তী সময়ে যা স্টালিনের তত্ত্ব
হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই আদর্শ একটি লৌহযুগের আদর্শ ছিল। অনেক বড় বড় উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল
এই আদর্শে। কিন্তু ট্র্যাজিক বিচ্যুতিও ঘটেছিল, যেমন নাকি হালফিলে জানা গেছে।
যারা ভবিষ্যতে ঝাঁপ দিতে চেষ্টা করার সাথে
সাথে ঢিলে করে ফেলে অতীতে তাদের পায়ের ভর, সাধারণতঃ তারা দুটোর মাঝের শূন্যে দোদুল্যমান
হয় আর প্রখর সূর্যের তাপে কুঁকড়ে যায়; বিশেষ করে হিমালয়ের দক্ষিণ দিকের যে তপ্ত সূর্য,
আমদানি করা ভাবনা ও উৎসাহে ফেঁপে ওঠা যুবদের অনেক প্রজন্মকে কুঁকড়ে ছেড়েছে। বিপ্লবগুলিরও
একই গতি হয় যখন তারা অতীতকে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক, দুদিকেই ঝেঁটিয়ে বিদেয় দিতে চায়,
‘পুরোনোপন্থী নৈতিকতা’ শুধু এই জন্য ছুঁড়ে ফেলতে চায় কেননা তা পুরোনো এবং যারা সবচেয়ে
জোর গলায় তার মুখপাত্র হয় তারা হিপোক্রিট। ফরাসি বিপ্লব যখন গর্ববোধ করল যে সে মুক্ত,
বন্ধনহীন এবং শুধু নিজের প্রতি দায়ী, আর তাই নৈতিকতার এবং দিনক্ষণের একটা নতুন ক্যালেন্ডার
তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করল তক্ষুনি সে ভূপতিত হল। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মানুষের একসাথে
বেঁচে থাকার পরম্পরা যে সাধারণজ্ঞানপ্রসূত নৈতিকতা গঠন করেছে, সেই নৈতিকতার মজবুত ভিত্তিটা
না থাকাতে পথ হারিয়ে ফেলল ফরাসি বিপ্লব। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের আতঙ্কে অপরাধীর সাথে নিরপরাধও
কাটা পড়ল – ফ্রান্স বেঁচে গেল, স্বাধীনতা হারিয়ে গেল। আমাদের সময়ের বিপ্লব যদি ইতিহাসের
এই শিক্ষার প্রতি আরো বেশি নজর দিত তাহলে নিদারূণভাবে তার অগ্রগতি রোধ করা ট্র্যাজিক
বিচ্যুতিগুলোর কয়েকটি এড়িয়ে যেতে পারত।
ইংল্যান্ডের বিপ্লব পতনের আগে পর্য্যন্ত কমই
কাব্যের সৃষ্টি করতে পেরেছিল, ফ্রান্সের বিপ্লব নাম করার মত একটিও নয়, রাশিয়ার বিপ্লবও
তার থেকে বেশি কিছু করতে পারেনি। অন্ততঃ আংশিকভাবে এর কারণ ছিল নিজেদের লেখকদের প্রতি
এইসব মহান আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি। ফ্রান্সের কোনো সাহিত্য নেই বলে নালিশ উঠেছিল। ‘ব্যবস্থা
গ্রহণ করা গৃহমন্ত্রীর কাজ’ বলে নেপোলিয়ন বিপ্লবের যোগ্য উত্তরাধিকারীর মত জবাব দিয়েছিলেন।
শিল্পকলার জগতে ‘একপাথুরে’ তত্ত্বটি শিল্পীদের প্রচারকর্তার শ্রেণিভুক্ত করল (সামন্ততান্ত্রিক
তত্ত্ব, সব মিলিয়ে কম ক্ষতিকারক ভাবে উইলিয়াম শেক্সপিয়র এবং তাঁর সহ-অভিনেতাদের বাজিকর
ও হাতুড়েদের শ্রেণিভক্ত করেছিল), কাজের ক্ষেত্রে কবিদের, খবরের কাগজের সম্পাদকীয়গুলোকে
গদ্য থেকে পদ্যে অনুবাদকারী হিসেবে ধরল। বলতে গেলে কবিকে চ্যাপ্টা করে, দ্বিমাত্রিক
প্রাণীতে রূপান্তরিত করে, তার ভিতর থেকে সমস্ত ব্যক্তিবাদী মাথামুন্ডু এবং তার নিজের
মনেরও বৈপরীত্য ও অন্তর্দৃষ্টি নিংড়ে বার করে নেওয়া হল। কিন্তু মুশকিল হল যে কবিতার
পক্ষে সবকিছুকে একই সময়ে দুই কোণ থেকে বা দ্বৈতবীক্ষণেই দেখা সম্ভব, polyphemus একচক্ষুতে
– এবং একপাথুরে কবি স্বাভাবিকভাবেই একচক্ষু হবে, বার্টনের শব্দে বলতে গেলে – গভীরতা,
বৈপরীত্য, আততি, সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত উবে যায়।
ফয়েজ এই পরিস্থিতি থেকে, যাকে বলে একটিও আঁচড়
না খেয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। তাঁর কাজের একটা অংশের সমালোচনা হতে পারত খুবই পরম্পরাগত
অথবা বিমূর্ত বলে; অন্য অংশ, যেখানে তিনি ‘প্রগতিশীল’ হওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কাব্যিক
থেকেও বেশি রাজনৈতিক হয়ে উঠছিল। কিছু সমালোচনা উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু
স্পষ্টতঃ অসাধরণ কবিতাগুলোতেও শেষের দিকে একটা টলে যাওয়া বা পড়ে যাওয়া টের পাওয়া যায়,
যেখানে মনে হয় ফয়েজ জোর করে তাঁর ভিতরের বেসুরগুলো মেলাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ঠিক
সুরটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না।
এতদিনে বিপ্লবের ইতিহাসে, আমাদের যুগে শিল্পীর
কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গঠন করা সম্ভব হয়ে যাওয়া উচিৎ। কবিতা প্রদর্শনীয় সত্য নিয়ে
কাজ করে না, ধাঁধা ও সন্দেহ, সম্ভাব্যতা ও জটিলতা নিয়ে কাজ করে। বেশি ব্যবহারিক মানুষেরা
যে পথ তৈরি করে দিয়েছেন সেই পথে প্রশ্নহীন, দিকনির্দেশকারী থামের মত দাঁড়িয়ে থাকা,
নিজেকে অনমনীয় একপাথুরেতে রূপান্তরিত করা লেখকের কাজ নয়। বরং কাজটা, রাষ্ট্রশক্তির
অংশ হিসেবে হোক বা কারাগারে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় হোক, প্রয়োজনীয় দায়িত্ববোধের সাথে, স্থায়ী
বিরোধীপক্ষের মত হয়ে আন্দোলনের সেবা করার কাজ। অভিজ্ঞতা একটু বেশিই স্পষ্ট করে দিয়েছে
যে সমাজবাদী দল এবং সরকারেরও নিতান্ত প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ বিরোধী পক্ষ। সমাজ পরিবর্তনকারী
শক্তিগুলিকে উদ্দীপিত করার কাজে শিল্পের কম ব্যস্ত থাকা উচিৎ - তাদের উদ্দীপিত করার
জন্য অন্যান্য বুনিয়াদি সংগঠনগুলি রয়েছে – শিল্পকে বরং ব্যস্ত থাকা উচিৎ নৈরাজ্য অথবা
পাশবিকতায় ওই শক্তিগুলির পতন রোধ করার কাজে।
এই কাজে তাকে অতীতের মূল্যবোধগুলির সংরক্ষক
হিসেবে দেখা যেতে পারে। বর্তমানের তোলপাড়ে অতীতের নীতিশাস্ত্র ততটাই অপরিহার্য যতটা,
রাজনীতিতে এবং অর্থনীতিতে এর আবিষ্কারগুলি। শিল্প একটি প্রাচীন ও নবীন সভ্যতার মাঝে
সংযোগ স্থাপনকারী; আর প্রাচ্যে, যেখানে কবিতা একটি জীবন্ত শক্তি সেখানে, সেই সমস্ত
কিছুকে প্রভাবিত করতে শিল্পের সক্ষম হওয়া উচিৎ যা ব্যবহারিক কাজের মানুষেরা মূর্খের
মত উপেক্ষা করবে। পুরোনোর মন্দের বিরুদ্ধে শিল্প হবে নতুনের দূত, আর নতুনের মন্দের
বিরুদ্ধে ঐতিহ্যগত বুদ্ধিমত্তার সংগ্রাহক, যে জানে যে অন্যায় ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই করা
হোক বা মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে, শেষ বিচারের দিন আসবেই। পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অবশ্যম্ভাবী
যে দ্বন্দ্বগুলোর আবির্ভাব, শিল্প সে দ্বন্দ্বগুলোর নিষ্পত্তি করতে সমাজকে সাহায্য
করবে এমন ভাণ করে নয় যে দ্বন্দ্বগুলো উবে গেছে, বরং দিনের আলোয় এবং কল্পনার আলোয় সে
দ্বন্দ্বগুলোকে এনে। এর জন্য প্রয়োজন শিল্পীর নিজের দৈনন্দিন চেতনায় ওই দ্বন্দ্বগুলো
অনুভব করা, যেমন নাকি সব মানুষেরাই অনুভব করে থাকে, একটু কম তীব্রতায়, আর একপাথুরেরা
করতে পারে না।
ফয়েজের প্রতি বিশ্বাস রাখা যেতে পারে যে তিনি
নিজের ক্ষমতাকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, এবং যেমন যেমন যুগের শিক্ষাগুলো বেরিয়ে
আসে তিনি তেমন তেমন সেগুলো গ্রহণ করেন। তাঁর কাছে যুগের ধাক্কা ও ভ্রমমুক্তিগুলো, সমাজবাদের
শিকল থেকে নয়, সমাজবাদের অর্থবিভ্রাটের শিকল থেকে মুক্তির মত মনে হওয়া উচিৎ। পুরাতনী
রূপে তাঁর উল্টোছবি – জাহাজের তরঙ্গপীড়িত ডেকে দৃঢ়সংকল্প অডিসিয়ুস, বিপদজনক শিলাখন্ডের
ওপর চুম্বকের মত টানতে থাকা বাঁশি – সরলীকরণ ছিল। যে সহজাত কু-বোধগুলিকে সে রামনাম
করে দূর করতে চাইছিল সেগুলো একেবারেই একপাথুরে ছিল না এবং একান্তই মনোগত ছিল। বাস্তবে
সেগুলো এমন কোনো পদচিহ্নের মত ছিল না যা থেকে বেরিয়ে যেতে, পিছনে ছেড়ে আসতে হবে। সেগুলোর
সাথে জড়িয়ে ছিল বাস্তবের অন্য এক প্রজাতি – অতীতের অনেক অনেক কিছু যা ভালো ছিল এবং
যার বাঁশির গানের প্রতি কান বন্ধ রাখা যাত্রীর পক্ষে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে। এখন
ফয়েজের হ্যাঁ-এবং-না, আরো বিশিষ্ট ও মৌলিক দ্বন্দ্বে বিকশিত হয়ে গিয়ে থাকবে। তাঁর চিন্তাভাবনার
মূলে রয়েছে মানুষের দৈত্যাকার কদমে এগিয়ে যাওয়ার অথবা দৈত্যাকার অপরাধে আত্মধ্বংসে
পতিত হওয়ার নতুন-পাওয়া ক্ষমতা। এই পরিস্থিতিতে একজন শিল্পীর একটি দলে থাকা এবং সব দলের
দোষত্রুটি ধরা উচিৎ।
[ভি.জি.কিয়ের্নান কৃত ফয়েজের কবিতার অনুবাদ গ্রন্থটির ভূমিকা – এডিনবরা,
২৪শে মার্চ, ১৯৫৭]